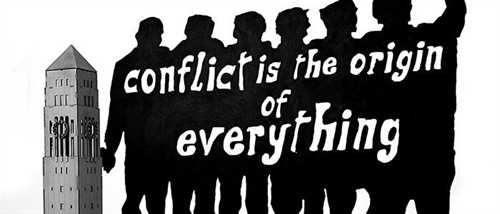“পুরাতন জিসিন কি ডিম পাড়ে?”- আসুন বেঁচে দিই!
“এ্যানিমেলস ইউনাইটেড” : মানুষের কর্তৃত্বের উপর প্রাণ – প্রকৃতির প্রতিরোধ
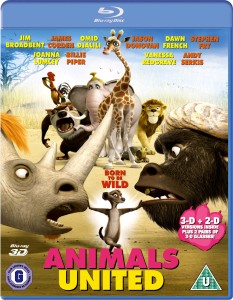
আফ্রিকার কোন একটি এলাকা- তৃণভূমি। যেখানে বছরে একটি নির্দিস্ট মৌসুমে পানি আসে একটি নদী থেকে। ঐ একটি মৌসুমের পানিতেই তাদের সারা বছরের খাদ্য এবং পানির যোগান হয়। কিন্তু, এ বছর নির্দিস্ট সময় অতিবাহিত হলেও এখনো পানি আসেনি। প্রাণীরা কম বেশি পানির সংকটে ভুগছে। শুরু হয়ে গেছে ২ টি প্রাণী গ্রুপের মধ্যে পানি নিয়ে ঝগড়া- স্বল্প পরিমাণ পানির উৎস নিয়ে। এমন পরিস্থিতিতে প্রথমেই সিংহ এবং তার বন্ধু (বেঁজি) পানির উৎসের খোঁজে বের হয়। পথের মধ্যে তাদের সাথে দেখা হয়- শ্বেত মেরু ভাল্লুক, অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙ্গারু, প্রায় ৭৫০ বছর ধরে জীবিত কচ্ছপ দম্পতি, টর্কিশ চিকেন প্রভৃতি প্রাণীর সাথে। অবশেষে তারা পানির উৎসের সন্ধান পায়, কিন্তু সেটি পাথর দিয়ে আবদ্ধ। যেটিকে আমরা (মানুষ) বলি ড্যাম্প বা বাঁধ। যা করা হয়েছে একটি ইকোট্যুরিজম এর নামে। এই ইকোট্যুরিজমে আবার বসেছে ১৬৮ তম জলবায়ু সম্মেলন। এই পার্কটিতে বানর, হাঙ্গর, সহ অল্প কিছু (সংখ্যায় এবং প্রজাতিতে) বিভিন্ন প্রাণীকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। যথারীতি সেখানে তারা বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় এবং সবশেষে সিংহ আটকা পড়ে। অন্যরা ফিরে যায় খালি হাতে তাদের জঙ্গলে।
সিনেমাটি আহমরি কিছু নয়। আইএমডিবি রেটিং মাত্র ৪.৯/১০। পরিচালক রেইনহার্ড ক্লস ও হগলার টেপ। কিন্তু সিনেমাটিতে একটি বড় ধরনের দর্শন এবং দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হয়েছে।

মানুষ বলে, তারা নাকি সৃষ্টির সেরা জীব, তাদের ক্ষমতা অসীম। তারা প্রকৃতির সকল বস্তুকে নিজের করায়ত্ত্বে করে নিজেকে সাংস্কৃতিক জীব হিসেবে রূপান্তর ঘটিয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র অনুজীব এর ক্ষমতা সম্পর্কে কী আদৌ অবগত আছে? শুধু চিন্তা করুন, যে সমস্ত ব্যকটেরিয়া আমাদের চারপাশের জৈব যৌগকে পঁচন ঘটায়। সে সমস্ত অনুজীব যদি নিজেদের কাজটুকু বন্ধ করে দেয়; কিংবা মনে করুন তারা অভিযোজন করে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে অন্য কিছুতে (পঁচানো বাদে) রুপান্তর করলো। ভাবুন একদিনেই আমাদের সভ্য পৃথিবী বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যাবে।
সহিষ্ণুতা : শৈশবেই শিখতে হবে প্রাণ ও প্রকৃতি থেকে
প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কেন সহিংস হচ্ছি বা সহিংস হয়ে পড়ছি? কিংবা কিভাবে আমাদের মধ্যে এই আচরণ তৈরি হচ্ছে? মনোবিজ্ঞান কিংবা আচরণ বিজ্ঞান হয়তো এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবে।
এ বিষয়ে আমার নিজের একটি ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাটা আপনি মানতেও পারেন আবার নাও মানতে পারেন। কিন্তু ব্যাখ্যাটা আমার কাছে যৌক্তিক মনে হয়েছে।

এভাবে আস্তে আস্তে এই সহিংসতা উদ্ভিদ এবং প্রাণী থেকে রূপান্তরিত হয় মানুষে। তাই আমরা ধরেই নিই যে, ছোট বোনটার চুল টেনে দেয়াটা অপরাধ নয় কিংবা দূর্বল বন্ধু কিংবা ছোটদেরকে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দেয়া কোন ব্যাপারই না! অন্যদের সাথে অকারণে মারামারি, ঝগড়া এগুলোও হয়ে ওঠে অনুসঙ্গ।
পরবর্তীতে বড় হওয়ার সাথে সাথে এই আচরণগুলো বড় হতে থাকে। বোনের উপর অত্যাচার রূপান্তুরিত হয় বউ কিংবা রাস্তায় হেটে যাওয়া মেয়েটার ক্ষেত্রে- নারী নির্যাতন বা অধুনা ‘ইভটিজিং’। ছোট-খাটো চুরি রূপান্তরিত হয় চাঁদাবাজি কিংবা ছিনতাই এ।
একটি বীজ বিদ্যাপীঠ
‘নবধান্যিয়া’ শব্দের অর্থ হচ্ছে নয়টি শস্য বীজ। নব=৯ আর ধান্যিয়া= শস্যবীজ। এটি একটি জীব বৈচিত্র্য খামার (Bio-Diversity Firm)। একই সাথে এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের-নাম ‘বীজ বিদ্যাপীঠ’ ইংরেজিতে বলা হয় ‘Earth University’। এই প্রতিষ্ঠানটির দাবি অনুযায়ী এটি একটি অর্গানিক বা জৈব কৃষি শিক্ষার আদর্শ স্থান।
প্রতিষ্ঠান এর নাম কেন নয়টি শস্য? এমন প্রশ্ন মাথায় আসা স্বাভাবিক। পরে জানলাম ‘নবধান্যিয়া’ এর শুরুর সময় প্রতিষ্ঠাতা ‘বন্দনা শিবা’ এই রামগড় গ্রামে দেশীয় বীজ সংগ্রহের জন্য বের হন। সারা দিন ঘুরে তিনি নয়টি শস্য বীজ সংগ্রহ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন দেখেন ৯ সংখ্যাটি একটি টেকসই বা স্থায়িত্বশীল সংখ্যা। গণিতের সর্বোচ্চ অঙ্ক। তাছাড়া ৯ সংখ্যাটিকে যত বার গুন করা হোক না কেন সেখানে ৯ এর অস্তিত্ব থাকবেই। যেমনঃ ৭X৭=৪৯; এখানে যেমন ৯ আছে। তেমনি ৭X৯=৬৩; ৬+৩=৯। ‘নবধান্যিয়া’ এর লোগো হচ্ছে ইংরেজি ৯; যা আবার বীজ দিয়ে তৈরি। এখানকার অনেক কিছুই ‘নবধান্যিয়া’ লোগো এর সাথে মিল রেখে করা হয়েছে। ‘নবধান্যিয়া’ এর নামকরণ এর ঘটনা কাকতালীয় মনে হলেও তারা এই নামটাকে যৌক্তিক এবং অর্থবোধক করে তুলেছে।
ভারতের উত্তরাখণ্ড প্রদেশের রাজধানী শহর দেরাদুন থেকে ১৬ কিমি দূরে রামগড় গ্রামে ৪৫ একর জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রবেশের শুরুতেই পড়বে বিশাল আম বাগান। মনে হবে বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জের কোন আম বাগানে প্রবেশ করছি। ৫ মিনিট হাটার পরে চোখে পড়বে প্রবেশ দ্বার ‘বীজ বিদ্যাপীঠে স্বাগতম’।
প্রবেশের পর প্রথেমেই একটি লেখাতে চোখ আঁটকে গেল ‘Coke Pepsi Free Zone’. পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বের হয়ে এসে স্বাগত জানালেন। এবং সহকর্মীর মাধ্যমে আমার রুম দেখিয়ে দিলেন। এটি কোন বড় বিল্ডিং নয়। ছোট ছোট একতলা ঘর। বাইরে থেকে প্লাস্টার বিহিন ইটের দেয়ালে লাল রঙ। কিন্তু ভিতরে প্রবেশের সাথে সাথে দ্বিধায় পরে গেলাম। কেননা ভেতর দেখে দেখে মনে হল মাটির দেয়াল। মাটি দিয়ে লেপা। পরে হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখলাম ইটের দেয়ালের ওপরে প্লাস্টার এবং রঙ না করে মাটি দিয়ে লেপানো। কিন্তু টয়লেট একবারে সুন্দর এবং আধুনিক।
যাইহোক, ফ্রেশ এবং অন্যান্য কাগুজে কাজ শেষে বের হলাম ‘নবধান্যিয়া জীব বৈচিত্র্য খামার/বীজ বিদ্যাপীঠ’ পরিদর্শনে। ম্যানেজার জে পি কালি পরিচয় করিয়ে দিলেন চন্দ্র শেখর ভাট এর সাথে। উনি কিছু ছেলে-মেয়েদের সাথে কাজ করছিলেন একটি মাঠে। ছেলে-মেয়েদের সাথে পরিচিত হয়ে জানতে পারলাম তারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছে এখানে ইন্টার্নশীপ করার জন্য। প্রথমে পরিচিত হলাম লিয়াট এর সাথে আমেরিকা থেকে ভারতে এসেছে ইন্টার্নশীপ করার জন্য। এটি তার গ্রাজুয়েশন এর একটি অংশ। তারপর শিবম; সবচেয়ে ছোট। দশম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে-দেরাদুনেই পড়ে। ওর গরমের ছুটিতে এসেছে এখানে এক মাসের জন্য। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি ‘নবধান্যিয়া’ থেকে এমন কোন একটি জিনিস শিখেছ যেটি তোমার সারাজীবনের জন্য কাজে লাগবে?’ ও বলল, ‘এখানে আসার পূর্বে আমি খুব দুষ্ট ছিলাম। কিন্তু, এখানে আসার পর আমি কেমন জানি বদলে গেছি।” গত সপ্তাহে রবিবারের ছুটিতে বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন আমাকে সবাই দেখে বলল, আমি নাকি ভালো হয়ে গেছি। এখানে এসে আমার কৃষির প্রতি আকর্ষণ জন্মেছে। আমি পড়াশুনা শেষ করে আমার বাবার সাথে কৃষি কাজ শুরু করবো’।
এর পরে পতিতপাবন চৌধুরী ওহম; ওড়িশ্যা থেকে এসেছে। সে ওড়িশ্যার একটি কলেজ থেকে বিবিএ করছে শেষ বর্ষের ইন্টার্নশীপ এর অংশ হিসেবে বীজ বিদ্যাপীঠ এ এক মাসের জন্য এসেছে। ওর আগ্রহের জায়গা মানব সম্পদ। ওর কৃষি এবং কৃষকদের নিয়ে একটি ড্রিম প্রজেক্ট রয়েছে এবং সেটি অর্গানিক কৃষিকে কেন্দ্র করেই।
ওহম এর সাথে ওর বন্ধু ধিরাজ মিশ্রা। কলকাতার ছেলে হলেও ওড়িশ্যায় বেড়ে ওঠা। ওর আগ্রহের জায়গা অর্গানিক কৃষির মার্কেটিং নিয়ে।
এই ৪জন ইন্টার্নকে সমন্বয় করছেন মিস প্রীতি। উনি পিএইচডি করছেন। পাশাপাশি বীজ বিদ্যাপীঠ এ প্রতিবেশ গবেষক হিসেবে কাজ করছেন। আমি বাংলাদেশ থেকে ৩ দিনের জন্য এই টিমের সাথে মিশে গিয়ে তাদের প্রতিদিনের কাজের সঙ্গী হলাম। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলাপ হবে।
চন্দ্র শেখর ভাট, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী আমাকে নিয়ে পুরো খামার ঘুরিয়ে নিয়ে দেখাতে বের হলেন এবং পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন খামার অন্যান্য কর্মীদের সাথে।পুরো খামারটি ৪৫ একর। একটি বড় অংশ আম বাগান। আম বাগানের ভিতরে থাকার জন্য কুঠির; এছাড়া প্রশাসনিক কাজের জন্য কয়েকটি কুঠির এবং শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বড় ডরমেটরি। সকালের মেডিটেশন, আড্ডা কিংবা অনানুষ্ঠানিক সভার জন্য রয়েছে খড়ের চালার গোলাকার ঘর। এই ঘরটির নাম গাজিবো। এটি সংস্কৃত এবং বুদ্ধ ধর্মের যৌথ সম্মিলন। শ্রদ্ধায় অবনত জ্ঞান কেন্দ্র। এখানে উন্মুক্ত জ্ঞান আহরণের সুযোগ তৈরি হয় বলে এমন নাম। গাজিবো নিয়ে মুগ্ধ হলাম যখন জানলাম- এটি তৈরি করা হয়েছে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ট্যাঙ্কের উপর। এর সাথে ডরমেটরির ছাঁদ এর সাথে সংযোগ রয়েছে। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এর চেয়ে ভালো হতো বলে আমার জানা নেই। যখন পানির সংকট থাকে তখন এই বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা হয়। (চলবে…)
ভালোবাসা ছড়িয়ে যাক প্রাণ ও প্রকৃতিতে!
১৪ ফেব্রুয়ারি। বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। প্রতিবছর সারা পৃথিবীর মানুষ ভালোবাসা দিবস উদযাপন করে ব্যক্তিক কিংবা সামষ্টিকভাবে। বিশেষ করে বয়োঃসন্ধিকালীন ছেলেমেয়ে এবং আপত তরুণদের মাঝে এই দিনটির বিশেষত্ব লক্ষ্যণীয়। এটির ইতিহাস, সাংস্কৃতিক পরিচয় কিংবা উদযাপনের ধরণ এবং ঢং নিয়ে রয়েছে হাজারো আলোচনা ও সমালোচনা। তবে সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হচ্ছে-এই দিনটিতে সারা পৃথিবীতে এক ধরনের ‘পজিটিভ ভাইভ’ বিরাজ করে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই পজিটিভ ভাইভটার খুব বেশি প্রয়োজন।
পৃথিবী তার সৃষ্টিলগ্নে ছিল উত্তপ্ত। তারপর ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকে। সেই শীতল অবস্থা থেকে এই সবুজ পৃথিবীর ‘সবুজ অধিবাসী’রাই পৃথিবীকে বাসযোগ্য উষ্ণ করে তুলেছে। সবুজ অধিবাসী বলতে পৃথিবীতে বিরাজমান লক্ষাধিক প্রাণকে বোঝানো হচ্ছে। তারা তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অর্থাৎ জীবনধারণ এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে বাসযোগ্য উষ্ণ করে তুলেছে। আজকের এই সভ্য পৃথিবীর দাবিদার যতটুকু মানুষ! ঠিক ততটুকুই কিংবা তারও অধিক দাবিদার বাদ বাকি প্রাণ। কিন্তু মানুষ নামক দাম্ভিক (!) প্রাণী নিজেকে ‘ফোকাস’ করতে গিয়ে আর সকল প্রাণকে ‘ডি-ফোকাস’ করে ফেলেছে। তাই তো পৃথিবীকে উষ্ণ করতে গিয়ে ধীরে ধীরে বৈশ্বিক উষ্ণতার মতো সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা’র জন্য প্রাকৃতিক কারণ এর সাথে শুধু মানুষ্য সৃষ্ট কারণই জড়িত। অন্য কোন প্রাণ এর জন্য দায়ি নয়। কিন্তু এই বৈশ্বিক উষ্ণতার মতো সমস্যা সমাধানে মানুষের প্রয়োজন পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল প্রাণীর সহযোগিতা।
বৈশ্বিক উষ্ণতা বলতে শুধু প্রাকৃতিক উষ্ণতাই নয়। এর সাথে সাথে সমাজিক-সাংস্কৃতিক উষ্ণতাকেও বিবেচনা করা হচ্ছে। দিনকে দিন এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সমান্তরালভাবে। যুদ্ধ, সন্ত্রাস, সামাজিক সহিংসতা, নির্যাতন, প্রতিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের মতো হাজোরো সমস্যায় জর্জরিত বর্তমান পৃথিবী এবং মানুষ। এই সমস্যার নেতিবাচক প্রভাব শুধু মানুষ একা ভোগ করছে না; অন্য প্রাণও সংকটের সম্মূখীন। কিন্তু একমাত্র মানুষই পারে এই সমস্যা থেকে উত্তোরণ করাতে। অন্য প্রাণ হতে পারে সহযোগী, সহযাত্রী; কিন্তু নেতৃত্ব মানুষকেই দিতে হবে।
ভালোবাসা দিবসে যে ‘পজিটিভ ভাইভ’ বিরাজ করে সেই পজিটিভ ভাইভটা হতে পারে এই বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক ধাপ। কিন্তু সেটি শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। আরো নির্দিষ্ট করে বললে শুধুই আমাদের ভালোবাসার মানুষ কিংবা সবচেয়ে নিকটজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেটি কী এই স্বল্প গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে? আসুন এই গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসি।
এই ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসা বিলিয়ে দেই আমাদের সবচেয়ে দূরত্বের সম্পর্কের মানুষের জন্য। যে ব্যক্তিটির সাথে আমাদের সবচেয়ে খারাপ সম্পর্ক; আসুন এই ভালোবাসা দিবসে তাকেই ভালোবাসি। তাকে একটি ফোন দিয়ে জানাই ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা। ভালোবাসা দিবসে আমরা ফুল ও চকলেট উপহার দিতে ভালোবাসি। সেই ‘শত্রু’কেই দিই ফুল আর চকলেট। দেখবো আমাদের জীবনটা আরো বেশি ভালোবাসায় ভরে উঠবে।
ভালোবাসা দিবসে আমরা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ভালোবাসা বিলিয়ে দিতে চাই। চলুন না বিলিয়ে দিই যার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা প্রয়োজন সেই মানুষটাকেই। হয়তো আপনার আমার পরিচিত কেউ মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত; তাকেই জানাই আমাদের ভালোবাসা। কিংবা আমাদের আশেপাশের হাজারো ভালোবাসা (!) বঞ্চিত মানুষ আছে- আসুন তাদেরকেই ভালোবাসি। ভালোবেসে ব্যবস্থা করি একবেলার খাবার- ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের পরিবর্তে। কিংবা প্রয়োজনীয় সেবা। আসুন ভালোবাসা দিবসে ছুটি নিয়ে-ভালোবাসার মানুষটিকে সঙ্গে নিয়ে সময় কাটাই কিছু ভালোবাসা বঞ্চিত নারী, শিশু এবং প্রবীণ নাগরিকের সাথে। ভালোবাসা দিবসে আসুন রক্ত দেই। কিংবা ব্যস্ত দিনের হাজারো ব্যস্ততার মাঝে একটি অন্তত ভালো কাজ করি।
ভালোবাসা কি শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? আমরা কী শুধু মানুষ নিয়েই বেঁচে থাকি? মানুষ ছাড়াও আমাদের চারপাশে হাজারো বস্তুগত এবং অবস্তুগত উপাদান রয়েছে। সেই সমস্ত উপাদানগুলোকে কি ভালোবাসা যায় না? আমরা যে বায়ু গ্রহণের মাধ্যমে বেঁচে আছি-সেই বায়ুকে চলুন ভালোবাসি। দূষিত বায়ুকে কম দূষিত করি (কম কার্বণ নিঃসরণ করা) কিংবা বিশুদ্ধ করার (গাছ লাগানো) উদ্যোগ নিয়ে বায়ুকে ভালোবাসি। আসুন মাটিকে ভালোবাসি; কম রাসায়নিক সার-কীটনাশক ব্যবহার কিংবা মাটি দূষণ কম করে।
ভালোবাসার অন্য এক প্রতিশব্দ হয়তো ফুল। আমরা প্রতিবার ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসার মানুষটিকে ফুল উপহার দিই-খুবই ভালো কথা। এবার ফুলটিকেই ভালোবেসে একটি ফুলগাছ লাগাই। যেন আগামী ভালোবাসা দিবসে ফুল কেনা না লাগে। কিংবা ভালোবেসে ভালোবাসার মানুষটিকেই হয়তো একটি ফুলগাছই উপহার দিলাম।
ভালোবাসা দিবসে অনেকেই মানবতার জন্য রক্তদান ক্যাম্প, চিকিৎসা ক্যাম্প, অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন করি। নিঃসন্দেহে খুবই ভালো উদ্যোগ। কিন্তু পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণীর জন্য স্বাস্থ্য ক্যাম্প কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় অর্থ সংগ্রহ করতে কী পারি না-এই ভালোবাসা দিবসটিকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে। আসুন ভালোবাসা দিবসে কিছু না পারি প্রাণ-প্রকৃতি-প্রতিবেশের অন্তত ক্ষতি হয় এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকি।
কেন ভালোবাসার এই গন্ডি ভাঙা জরুরি? কারণ মানুষ একা বাঁচতে পারে না। আর তাই মানুষের প্রয়োজনেই মানুষের পাশাপাশি অন্য প্রাণ এবং প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিক্ষা দিক এই সার্বজনীন ভালোবাসা দিবস। এই দিনের ‘পজিটিভ ভাইভ’ একটি নির্দিষ্ট গন্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে আরো বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে দিতে পারলেই এই দিনটির প্রকৃত তাৎপর্য ফুটে উঠবে। পাশপাশি, শুধু মানুষে-মানুষে সীমাবদ্ধ থাকলে এক সময় মানুষ ছাড়া আমাদের চারপাশে আর কিছুই থাকবে না। আবার শুধু ভালোবাসার মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে আমাদের শত্রু সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। তাই ভালোবাসাতে হবে সবাইকে। আমাদের শত্রুকে; ভালোবাসা বঞ্চিত মানুষটিকেই। ভালোবাসতে হবে আমাদের চারপাশের প্রাণ, প্রকৃতি এবং প্রতিবেশকে। তবেই সম্ভব একটি ভালোবাসাময় পৃথিবীর। যেটি হবে আরো বেশি উপযোগী, স্বাচ্ছন্দ্য এবং টেকসই সকল প্রাণের জন্য।
বৈশ্বিক উষ্ণতা বলতে শুধু প্রাকৃতিক উষ্ণতাই নয়। এর সাথে সাথে সমাজিক-সাংস্কৃতিক উষ্ণতাকেও বিবেচনা করা হচ্ছে। দিনকে দিন এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সমান্তরালভাবে। যুদ্ধ, সন্ত্রাস, সামাজিক সহিংসতা, নির্যাতন, প্রতিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের মতো হাজোরো সমস্যায় জর্জরিত বর্তমান পৃথিবী এবং মানুষ। এই সমস্যার নেতিবাচক প্রভাব শুধু মানুষ একা ভোগ করছে না; অন্য প্রাণও সংকটের সম্মূখীন। কিন্তু একমাত্র মানুষই পারে এই সমস্যা থেকে উত্তোরণ করাতে। অন্য প্রাণ হতে পারে সহযোগী, সহযাত্রী; কিন্তু নেতৃত্ব মানুষকেই দিতে হবে।
ভালোবাসা দিবসে যে ‘পজিটিভ ভাইভ’ বিরাজ করে সেই পজিটিভ ভাইভটা হতে পারে এই বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক ধাপ। কিন্তু সেটি শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। আরো নির্দিষ্ট করে বললে শুধুই আমাদের ভালোবাসার মানুষ কিংবা সবচেয়ে নিকটজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেটি কী এই স্বল্প গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে? আসুন এই গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসি।
ভালোবাসা কি শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? আমরা কী শুধু মানুষ নিয়েই বেঁচে থাকি? মানুষ ছাড়াও আমাদের চারপাশে হাজারো বস্তুগত এবং অবস্তুগত উপাদান রয়েছে। সেই সমস্ত উপাদানগুলোকে কি ভালোবাসা যায় না? আমরা যে বায়ু গ্রহণের মাধ্যমে বেঁচে আছি-সেই বায়ুকে চলুন ভালোবাসি। দূষিত বায়ুকে কম দূষিত করি (কম কার্বণ নিঃসরণ করা) কিংবা বিশুদ্ধ করার (গাছ লাগানো) উদ্যোগ নিয়ে বায়ুকে ভালোবাসি। আসুন মাটিকে ভালোবাসি; কম রাসায়নিক সার-কীটনাশক ব্যবহার কিংবা মাটি দূষণ কম করে।
ভালোবাসা দিবসে অনেকেই মানবতার জন্য রক্তদান ক্যাম্প, চিকিৎসা ক্যাম্প, অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন করি। নিঃসন্দেহে খুবই ভালো উদ্যোগ। কিন্তু পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণীর জন্য স্বাস্থ্য ক্যাম্প কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় অর্থ সংগ্রহ করতে কী পারি না-এই ভালোবাসা দিবসটিকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে। আসুন ভালোবাসা দিবসে কিছু না পারি প্রাণ-প্রকৃতি-প্রতিবেশের অন্তত ক্ষতি হয় এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকি।
দ্বন্দ্ব ও উন্নয়ন (Conflict and Development)
দ্বন্দ এবং উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করার আগে দ্বন্দ্ব কে নিয়ে একটু নাড়াচড়া করা জরুরি। প্রথমেই জেনে নেই দ্বন্দ্ব এর সংজ্ঞা এবং ধরণ সমূহ।
Conflict শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয় ‘দ্বন্দ্ব’ শব্দটি। দ্বন্দ্ব বলতে বুঝায় সংঘাত, ঝগড়া, বিবাদ, যুদ্ধ বা শত্রুতা; দ্বিধা বা সংশয়। দ্বন্দ্ব হলো বৈপরীত্য বা Contradiction। দ্বন্দ্ব একটি সমাজ এবং সংস্কৃতিতে গতিশীলতা দান করে। সবকিছু নিয়ত গতিশীল, তা সে অণু-পরমাণুই হোক কিংবা গ্রহ-নক্ষত্র। আমরা আমাদের সীমিত খালি চোখে তা সবসময় অনুধাবন করি না। এবং এই গতিশীলতার মধ্যে বৈপরীত্য কাজ করে। আর এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সবকিছুর বিকাশ হয়। সে জন্যই কোন কিছু বিকাশের কিংবা পরিবর্তনের পথ কখনো মসৃণ হয় না। ধীরে ধীরে জড়ো হওয়া ছোট ছোট পরিবর্তন হঠাৎ করে বড় পরিবর্তনের সূচনা করে।
মানুষের সৃষ্টি থেকেই দ্বন্দ্বের শুরু। কখনো সে নিজের সাথে। কখনো বা অন্যের সাথে। আমাদের চারপাশের প্রতিদিনকার ঘটনাগুলো লক্ষ্য করলে আমরা দ্বন্দ্বের নানারূপ দেখতে পাই। কিছু সাধারণ দ্বন্দে¦র রূপ হচ্ছে-গোত্র-গোত্র দ্বন্দ্ব, জাতিগোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, নারী-পুরুষ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, মতাদৈর্শ্বিক দ্বন্দ্ব (বামপন্থী বনাম ডানপন্থী), মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব (গার্মেন্টস কর্মী এবং মালিক)। কখনো কখনো এই দ্বন্দ্বের কারণ হয় বস্তুগত উপাদান নিয়ে। যেমন: প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমি নিয়ে চরাঞ্চলগুলো প্রায়ই দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। আবার সাংস্কৃতিক উপাদান নিয়েও দ্বন্দ্বের সংখ্যা কম নয়। উদাহরণ হিসেবে ভাষা নিয়ে দ্বন্দ্ব, সম্মান-প্রতিপত্তি নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, প্রভৃতি।
দ্বন্দ্বকে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়। ধারণা করা হয়, শুধুমাত্র মানুষে মানুষেই দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতির প্রায় অধিকাংশ বিষয়ের সাথে দ্বন্দ্ব অপরিহার্য একটি বিষয়। মানুষে মানুষে যেমন দ্বন্দ্ব থাকে তেমনি দ্বন্দ্ব হয় মানুষ এবং প্রকৃতির সাথে। আবার প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের সাথে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি এবং পদ্ধতি এক নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মানুষ এবং প্রাণীর মধ্যে যে ধরনের দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল, মানুষ এবং উদ্ভিদের সাথে ভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল। আবার ভৌত উপাদান মাটি, পানি, বায়ুর সাথে ভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। আমরা যদি বায়ুকে দূষিত করে ফেলি আমাদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাহলে একসময় ওই বায়ু আর আমাদের জীবন প্রদায়ী না হয়ে হুমকির কারণ হয়ে যায়। তখন আমরাই আবার নানাভাবে সেই বায়ুকে নিজেদের জীবন উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করি।
মানুষ ছাড়াও অন্যান্য জৈবিক এবং ভৌত পরিবেশের একটি উপাদানের সাথে অন্যটির নানা ধরনের দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। আবার একটি প্রাণীর সাথে উদ্ভিদের যে দ্বন্দ্ব, সেটি উদ্ভিদে-উদ্ভিদে বা প্রাণীতে-প্রাণীতে ভিন্ন হয়। আবার একই উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে প্রজাতি ভেদেও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থকতে পারে। সবশেষে পরিবেশের ভৌত বা জৈবিক উপাদানের সাথে জড় উপাদানের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল। আবার জড় বস্তুর মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। যেমন: প্রযুক্তি হিসেবে লাঙল এর ব্যবহার কমে যায় যখন কৃষি ক্ষেত্রে পাওয়ার ট্রিলার এর আর্বিভাব হয়। অন্যদিকে জড় বস্তুর ব্যবহারের সাপেক্ষে পরিবেশের জৈবিক উপাদানের সাথে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তৈরি হয়। পাওয়ার ট্রিলার দিয়ে ভূমি কর্ষণের ফলে মাটিস্থ কেঁচোসহ অন্যান্য উপকারী কীট-পতঙ্গ নষ্ট হচ্ছে। আবার কার্বন নিঃসরণের মাধ্যমে বায়ু দূষণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
দ্বন্দ্বকে যদি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়। আর উন্নয়ন যদি আর্থ-সামাজিক নির্দেশকের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়। তাহলে দ্বন্দ্ব উন্নয়নেরই একটি অংশ। আবার কোন একটি জনগোষ্ঠীর দ্বন্দ্বগুলো না বুঝতে পারলে সেই জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে। আর এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিবেচনা না করাই বুঝি কাংখিত উন্নয়নের পথে আমাদের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। ধরা যাক, কোন একটি প্রান্তিক এবং সুবিধা বঞ্চিত(!) একটি জনগোষ্ঠীর জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হলো। কিন্তু, এখানে ওই জনগোষ্ঠীর সাথে আর যে সমস্ত জনগোষ্ঠীর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে তারা উন্নয়ন পরিকল্পনার বাইরে থাকে। তাহলে প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো কী আদৌও কার্যকর হবে?
অন্যদিকে উন্নয়নে যদি মানুষ-মানুষ ছাড়া প্রকৃতির অন্যান্য দ্বন্দ্ব গুলোকে বিবেচনা না করা হয়; তাহলে সেটি টেকসই উন্নয়ন হবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে বরেন্দ্র এলাকার খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করার জন্য ধান চাষভিত্তিক প্রযুক্তির অবতারণা এই প্রতিবেশীয় ধান এবং অন্যান্য প্রজাতি কিংবা পানি এবং মাটির যে সম্পর্ক সেটি ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করেছে। কিংবা ধান চাষ বৃদ্ধির ফলে ঐ এলাকার অচাষকৃত খাদ্য হিসেবে বিবেচিত উদ্ভিদ প্রজাতির ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে-সেটিও বিবেচনা করা জরুরি। যদি এই বিষয়গুলো বিবেচনা না করা হয় তবে সেটি তাৎক্ষণিক সুফল বয়ে আনলেও দীর্ঘমেয়াদে নানা ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাবে।
উদাহরণ হিসেবে জেন্ডার উন্নয়ন বলতে এখনো পর্যন্ত প্রধানতম ধারণা হচ্ছে জেন্ডার মানেই নারী। যার সকল কিছুতে নারী সম্পৃক্ত থাকবে। অনেকটা এভাবে বলা যায়, নারীদের জন্য নারীদের দ্বারা পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রম। এখানে শুধু পুরুষরা বাইরে থাকে তাই নয়; অনেকাংশে পুরুষকে জেন্ডার সমতার পরিপন্থি বা অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু, অন্যান্য বিষয়ের মতো নারী পুরুষের সম্পর্ক চিরকালই দ্বন্দ্বিক। তাই জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ এর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিবেচনা করাটা আত্যাবশ্যকীয়।
নোট: ছবিগুলো ইন্টানেট এর মুক্ত সোর্স থেকে সংগৃহীত।
চলো প্রশ্ন করি
এখনও বাবা-মা, শিক্ষকরা বলেন, ‘মানুষ হ’! আমিও মানুষ তারাও মানুষ।
কিন্তু, সেই মানুষগুলোর সাথে আমার
কত আকাশ পাতাল পার্থক্য। এই ধর, ক্রিকেটার সাকিব
আল হাসানের কথা- বয়সে বুঝি আমার সমান হবে। কিন্তু কোথায় সে আর কোথায় আমি? তাকে সবাই এক নামে চেনে। আর আমি কোথাকার কে? তাকে সবাই পূজা করে (বাংলালিংকের ভাষায়- প্রিয়জনেরা একটু
বেশিই পায়।), আর আমাকে খোঁচা মারে!
বাংলাদেশের প্রথম সঙ্গীত বিষয়ক টিভি অনুষ্ঠানের (ক্লোজ আপ ১ তোমাকেই খুঁজছে
বাংলাদেশ) ‘থিম সং’ হচ্ছে,
আছে। প্রতি রাতে কত হাজারো স্বপ্ন দেখি। কিন্তু, ঘুম ভাঙলেই দেখি বিছানায়- প্রকৃতির প্রবল আহবান! তাহলে ‘স্বপ্ন’ কী? ছোট বেলায় স্বপ্ন নিয়ে একটা লেখায় পড়েছিলাম, ‘মানুষ ঘুমিয়ে যত দীর্ঘ স্বপ্নই দেখুক, তার স্থায়িত্ব ৯ সেকেন্ড! স্বপ্ন নাকি আবার বর্ণান্ধ (কালার
ব্লাইন্ড)। স্বপ্নে নাকি রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ নেই। তাহলে
স্বপ্ন কী? ঘুম ভাঙলেই দেখি স্বপ্ন
টুটে (ভেঙে) যায়। তাহলে স্বপ্ন অটুট হবে কী করে?
আছে। সে মনে করে, ‘তার জীবনে কী ঘটবে?
তা নাকি আল্লাহ পূর্বেই তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে
জানিয়ে দেয়।’ তাহলে সাকিব আল হাসান,
নীল আর্মস্ট্রং, কলম্বাস, স্যার আইজাক
নিউটন এদেরও কী সৃষ্টিকর্তা স্বপ্নে এসে বলে দিয়েছিলেন? আমাকে কেন দেন না? আমার কী অপরাধ? আমিও তো অনেক বড় হতে চাই!
আমিও অনেক কিছু করতে চাই!
মুসলমান রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবুল কালাম আজাদ এর নাম আমরা সবাই জানি। তিনি ভারতের
একজন পরমাণু বিজ্ঞানীও। তার সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। তিনি নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান
ঘরে জন্ম গ্রহণ করেও দেশের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ছিলেন। তাকে স্কুলে বসতে
দেয়া হতো না। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে স্কুলের ক্লাস করতেন। তিনি অনেক
সুন্দর সুন্দর কথার মাধ্যমে তার জীবনের গল্প শুনিয়েছেন। তার স্বপ্ন নিয়ে একটা
সুন্দর কথা রয়েছে-
সম্ভবত, এ.পি. জে. আবুল কালাম
আজাদ এর স্বপ্ন ছিল এমন। যে স্বপ্ন তাকে ঘুমাতে দিত না। যে স্বপ্নের ফলে তিনি
দিনের চব্বিশ ঘন্টা সময়কে টেনে ৪৮ ঘন্টা করেছিলেন। আর তাই আজ তিনি স্বপ্ন দেখেন
না। স্বপ্ন দেখান। তাই আমাদেরও তার স্বপ্নের সাথে মিলিয়ে স্বপ্ন দেখতে হবে।
বসতে, ঘুমাতে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। কিন্তু, কী স্বপ্ন দেখব? কেমন স্বপ্ন? কিসের স্বপ্ন?
মুহাম্মদ (সঃ) ‘নবুয়াত’ পেলেন? কীভাবে নিউটন ‘মধ্যাকর্ষণ’ শক্তি আবিষ্কার
করলেন? কীভাবে মোহনদাস করমচাঁদ
গান্ধী ‘মহাত্মা’ হলেন? এই ৩ জনের নাম,
পরিচয়, ধর্ম এবং দেশ ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে কিন্তু একটা বড় মিল রয়েছে। আর সেটি
হচ্ছে- তারা ‘প্রশ্ন’ করতে পারতেন। খুবই আশ্চর্য তাই না?
একজন সাধারণ মানুষ এত বড় অসাধারণ হতে পারে? আমি ক্লাসে প্রশ্ন করলেই শিক্ষক বলেন, ‘গাধা’! বোকার মত প্রশ্ন
করিস কেন? মুখটা তখন কালো হয়ে যায়।
মা-বাবাকে প্রশ্ন করলে ধমক দিয়ে বলেন, বেয়াদপ! বড্ড পেঁকে গেছো! তখন মনে মনে কান ধরে বলি, জীবনে আর কখনো কাউকে মরে গেলেও প্রশ্ন কররো না। তাইতো
বিশ্বাস হয় না! কীভাবে একজন মানুষ প্রশ্ন করার মাধ্যমে বড় হতে পারে?
করলো? কে এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি
করলো?’ এই প্রশ্ন তিনি কার কাছে
করেছিলেন? হয়তো তার সহপাঠী, বন্ধু কিংবা চাচা অথবা বয়স্ক কারও কাছে। তারা কী করলো?
ভাবল। তিনি কী প্রশ্ন করা বন্ধ করলেন? না তিনি যখন অন্য কোথাও তার প্রশ্নের উত্তর পেলেন না। তখন তিনি নিজের কাছে
প্রশ্ন করলেন? শুধু নিজের কাছে প্রশ্ন
করে বসে থাকলেন না। নিজে নিজে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলেন এবং
প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়ে হয়ে গেলেন ‘বিশ্বনবী’, ‘মহানবী’। অর্থাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন নিজের কাছে।
নিউটন প্রশ্ন করলেন, ‘কেন আপেল নিচে পড়ল?
এত জায়গা থাকতে কেন আপেলকে নিচে আসতে হবে?
আপেল নিচে নামার প্রশ্নের উত্তর যখন খুঁজে
পেলেন তখন তিনি হয়ে গেলেন তার সময়কার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনিও বড় হলেন নিজেকে
প্রশ্ন এবং উত্তর খোঁজার মাধ্যমে।
দক্ষিন আফ্রিকায় ছিলেন। তখন তিনি সেখানকার এক রেলস্টেশনে চরম লাঞ্ছনার শিকার হন।
সেই রেলস্টেশনের প্লাটফর্মের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল,
সাথে পশুরমত আচরণ। তার মন কেঁদে উঠল। কেন এমন হবে? তিনি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য প্রচার করলেন অহিংসার
বানী। কোন পাশবিক যুদ্ধ, বিগ্রহ, বিদ্রোহ নয়। তাই তো তিনি আজ ‘মহান+আত্মা’= ‘মহাত্মা’।
নিজের কাছে। আর একটা বিষয় প্রশ্ন ভুল, অবান্তর বা অযৌক্তিক নয়। প্রশ্ন প্রশ্নই। ভাল প্রশ্ন, খারাপ প্রশ্ন বলে কিছু নেই। তাই মনে কোন দ্বিধা, সংশয়, সন্দেহ এর উদয়
হলেই প্রশ্ন করো। আর প্রশ্ন করে বসে থাকলে হবে না। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের
করতে হবে, যেভাবেই হোক (by hook or crook)। নুবাবা-মায়ের কাছে অনুরোধ- আপনাদের সন্তান যদি বেশি প্রশ্ন
করে। তবে বিরক্ত হবেন না। দয়া করে আপনার সন্তানকে বকবেন না। বরঞ্চ, প্রশ্ন করতে
উদ্বুদ্ধ করুন এবং তাকেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করবেন। দেখবেন সে নিশ্চয়
পারবে এবং ভবিষ্যৎ প্রশ্নের জন্য আপনাকে বিরক্ত করবে না। নিজে নিজেই খুঁজে
নেবে।
লাভ? অনেক লাভ! নিজের শক্তি-সামর্থ্য, নিজের সম্পদ-সম্পত্তি, আত্মবিশ্বাস-আত্মতৃপ্তি সবকিছুই খুঁজে পাওয়া যায়- প্রশ্নের
উত্তর খোঁজার মাধ্যমে। নিজের হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয়। তাই তো, এভারেস্ট বিজয়ী মুসা ইব্রাহীম দৃঢ় চিত্তে বলেন,- ‘পৃথিবীর একজন মানুষও যদি পারে। তাহলে মুসা ইব্রাহিমও পারবে।’
খুব সহজ? কক্ষনোই না! তোমার মনে যে
প্রশ্ন। তার উত্তর বাজারে প্রচলিত কোন গাইড বইয়ে নেই। যে বাজর থেকে গাইড বই কিনে
এনে উত্তর খুঁজে পেলাম। আর মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখে দিলাম। ব্যস, পেয়ে গেলাম গোল্ডেন ‘এ’ প্লাস।
পরতে পরতে লুকায়িত। খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্ট সাধ্য। সাপের মাথার মানিকের মত। এই
প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পৃথিবীর নিয়ম ভাঙতে হয়। এ.পি.জে. আবুল কালাম আজাদ এর আরেকটি
কথায় ফিরে যাই। তিনি বলেছেন, ‘পৃথিবীতে কিছু
মানুষের জন্ম হয় পৃথিবীর নিয়ম মেনে চলতে। আর কিছু মানুষের জন্ম হয় পৃথিবীর নিয়ম
ভাঙতে। আমার দরকার নিয়ম ভাঙার মানুষ গুলোকে।’
ঠিক নয়। নতুন কিছু হতে পারে আরো সঠিক বা
যর্থার্থ। তাইতো, আমাদেরকে নিয়ম ভাঙার দলে
ভিড়তে হবে। ভাবতে হবে নতুন কিছু। হতে হবে সৃজনশীল, কৌশলী। দৃঢ় প্রত্যাশার (প্রত্যয়+আশা)সাথে থাকবে আত্মবিশ্বাস;
হতে হবে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ- অবশ্যই নিজের কাছে।
হতে হবে পরমতসহিষ্ণু, শ্রদ্ধাশীল, উদার এবং বিশ্বজনীন। নিজেকে ভাঙতে হবে, গড়তে হবে। তাহলে হয়তো পৌঁছে যেত পারবো আমার অটুট লক্ষ্যে।
(সূত্র) আবিষ্কার করে ফেললাম। এখন পানি দিয়ে গিলে দেখি বড় হতে পারি কী না?
…..যদি বড় হতে পারি! তাহলে, বড় হওয়ার গল্প শোনাব আর…. একদিন…….।
নাম-১: ধর্ম নিরপেক্ষ নামের সন্ধানে
চিরস্থায়ী বস্তু। আকজন মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালবাসে তার নামকে। বিশ্বাস না হয়। কারো
নামে গালি দিয়ে দেখতে পারেন।
সক্রেটিস, আইনস্টাইন কে দেখি নি। তবুও তারা আমাদের কত পরিচিত। আপনি
একদিন থাকবেন না; কিন্তু আপনার নাম কিছুদিন
হলেও থাকবে (নুন্যতম ৩ প্রজন্ম পর্যন্ত)।
সন্ধানে
কোন লিঙ্গের)। আমি শুনেই মনে হল তিনি হিন্দু, তাই দিদি বলে সম্বোধন করে বিব্রত হলাম। আচ্ছা, কোন মানুষের নাম শোনার সাথে সাথে ধর্মের বিষয়টি আমার অবচেতন
মনে আসলো কেন? আচ্ছা ধর্মের বিসয় আসলেও
কেন তা সম্বোধনের সাথে সম্পর্কিত। তার নামে নাম কি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে
ধর্মকে প্রতিনিধিত্ব করে?
তো এরা কোন ধর্মের?
ঝালর বহন করে না। তাহলে কি নামের সাথে
ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই?
নামের পদবি নানা ভাবে সময়ের পরিক্রমায় নির্ধারিত হয়। যেমন ধরেন গাজী, শাহ, প্রভৃতি। এখন
এগুলোর সাথে ধর্মের যোগসাজস কোথায়?
পরিচয় হলাম, আমার নাম বলার পর তিনি
বললেন তন্ময়। আমি ভাই হিসবে সম্বোধন করলাম এবং দেখ হলে সালাম দিতাম। পরে জানলাম,
তার নাম তন্ময় কর্মকার। এখন আর সালাম দিতে পারি
না এবং দাদা বলে ডাকার চেস্টা করি।
নাকি বোঝা যায় কোন ধর্মের অনুসারী। একসময় বাংলায় মুসলমানদের নামের আগে মোঃ ব্যবহৃত
হত আর হিন্দুদের ক্ষেত্রে শ্রী। যদিও এখন সবায় সেতা ব্যবহার করতে অনেক অনীহা দেখা
যায়।
মানুষের ধর্ম সম্পর্কে কি নিশ্চিত হতে পারি?
লেখাটাকে সমৃদ্ধ করবে।
বোরখা, রোকেয়া এবং আমরা
যাইহোক, দুজনে সকালের খাবারের জন্য রুটি আর ডাল-ভাজি অর্ডার দিল। আমাদের অর্ডার আগে আসতে দেরি হচ্ছে। আমি বসে থেকে আশে পাশে দেখছিলাম (এটা আমার একটা অভ্যাস-খারাপ কি ভাল জানি না। সব কিছু-মানুষের খাওয়া, কথা বলা কিংবা কাজ করা প্রভৃতি।) ইতমধ্যে, একজন পুরুষ সম্ভবত আইসিডিডিআর’বি- এর স্টাফ (আইডি কার্ডের ফিতা দেখে তাই মনে হোল) এসে সেই নারী-পুরুষের টেবিলে বসল। নতুন আগত ব্যক্তি এই ক্যান্টিনের নিয়মিত কাস্টমার। উনি ওনার প্রতিদিনের স্বাভাবিক আচরণে কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নাস্তা করতে লাগলেন।
এই পরিস্থিতিতে অস্বস্তিতে পড়লেন নারীটি। পুরুষটি ফোনে কথা বলতে বলতে খাইতে লাগলেন আর নারীটি কি করবে? না করবে? পুরুষ টি খেতে লাগলেন নির্দ্বিধায়- আর নারীটি অনেক ভেবে চিন্তে ধীরে ধীরে রুটির টুকরো ছিড়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরে নেকাব তুলে আস্তে আস্তে মুখে দিলেন। রুটি ডাল ছাড়া। একটু প্ররে পুরুষটি কে তার ডালের বাটিটাও এগিয়ে দিলেন। নারীটি দুটি তন্দুর রুটি কোন কিছু ছাড়াই শুকনো খেয়ে ফেললেন।
কি এমন বিশ্বাস যে তাকে এই ধরনের আচরণে বাধ্য করলো। জীবন ধারনের জন্য খাওয়ার চেয়ে নেকাব রক্ষা করা কি এতই জরুরী। তিনি একান্ত বাধ্য না হলে নিশ্চিত এই পুরুষ সমাগত হোটেলে আসতেন না। কিংবা আমরা পুরুষরা কিভাবে নির্বিচার ভাবে নিজেদের উদার পূর্তিতে ব্যস্ত।
এই ঘটনা আমার দেখা এই প্রথম না।এবং শুধু মধ্যবয়সী কিংবা পৌঢ় নয়; তরুণ এবং নতুন মেয়েদের ক্ষেত্রেও (যারা শহুরে জীবনের এবং তথাকথিত ‘আধুনিক’ শিক্ষায় শিক্ষিত)।
অনেক আগে যখন রোকেয়া সমগ্র পড়েছিলাম। এখন ঘটনা টা ঠিক হুবহু মনে নাই। কিন্তু যতদূর মনে আছে উনি ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন। একজন পর্দায় আবৃত নারী বিপদে পড়েছেন। কিন্তু পর্দা নষ্ট হবে বলে তার সহযাত্রী এবং বিপদাক্রান্ত নারী নিজেও কাউকে সাহায্য করতে দিচ্ছেন না।
বেগম রোকেয়ার যুগ এখন আর নাই। কিংবা আমরা পুরুষরা আমাদের সুখ- সুবিধা গুলো দেখছি। কিন্তু আমাদের আর একটি অংশকে পর্দার নামে বাইরে বের করে মানসিক অত্যাচার করছি কি না? নিজের বিবেক বারবার সেই প্রশ্ন করছে আমাকে।